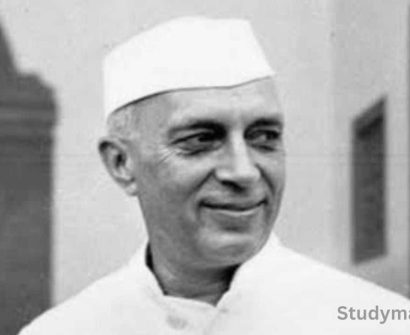ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ বা পটভূমি ব্যাখ্যা করো।
ঠান্ডা লড়াই এর উদ্ভব ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মত পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত দেশগুলির সরকারকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব সমসাময়িক কালে বলশেভিক নেতা তথা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান লেলিনের সহযোগী কমিউনিস্ট নেতা ট্রটস্কি ঘোষণা করেন যে হয় রুশ বিপ্লব ইওরোপে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করবে, নতুবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপীয় শক্তিগুলি মিলে রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করবে।
বস্তুতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার দিক থেকে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের প্রসারের আশঙ্কা এবং তার থেকেও বেশী করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিশ্বের বৃহত্তর অংশে বজায় রাখার প্রবল ইচ্ছা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইত্যাদি) ১৯১৭-১৮ সাল থেকেই রাশিয়া বিরোধী অবস্থান নিতে বাধ্য করেছিল। জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট লিটোভস্কের চুক্তি সম্পাদন করে যুদ্ধমধ্যেই রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে যাওয়াকেও পশ্চিমী জোট ভালো চোখে দেখে নি। ফলত ১৯১৮ সালে রাশিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড বলশেভিক রেড আর্মির বিরুদ্ধে জারের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী হোয়াইট আর্মিকে সৈন্য ও রসদ পাঠিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিতে থাকে, যদিও এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরাই জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারস্পরিক স্বপ্নের প্রেক্ষিতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের কারণ বা পটভূমি ছিল হিটলারের প্রতি তোষণ নীতি।
 |
| ঠান্ডা যুদ্ধ / ঠান্ডা লড়াই (Cold War) |
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনার প্রাক্কালে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া এবং হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসী জার্মানি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে যা মোলোটভ রিবেনট্রপ চুক্তি নামেও পরিচিত। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯৪১’র ১৪ই জুন ইউক্রেন অঞ্চল দখলের জন্য অপারেশন বারবারোসার মাধ্যমে হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন, তথাপি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সহ পশ্চিমী দুনিয়া এই অনাক্রমণ চুক্তিকে ভালো চোখে দেখেনি। অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এবং ফরাসী রাষ্ট্রপ্রধান দালাদিয়ের গৃহীত নাৎসীদের প্রতি তোষণ নীতিও রাশিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছিল পারস্পরিক অবিশ্বাসের এই বাতাবড়নে জার্মানির দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত রাশিয়া বাধ্য হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে মিত্রপক্ষে যোগদান করে যুদ্ধ করতে।
আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে নাৎসী জার্মানির ক্রমিক আগ্রাসন এই পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং রাশিয়াকে পরস্পরের কাছে আসতে বাধ্য করেছিল। জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে ব্রিটেন রাশিয়াকে আগাম সতর্কবার্তা পাঠয়েছিল এবং রাশিয়া জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পরেও ৭ই জুলাই চার্চিল স্তালিনকে নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী সব রকম সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হাতে রাশিয়া পরাজিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিপদ বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট তার ব্যক্তিগত দূত হ্যারি হপকিন্সকে মস্কোতে স্তালিনের কাছে পাঠান এবং যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে দেখা যায় যে ‘নাৎসীফোবিয়া’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং রাশিয়াকে কাছাকাছি এনেছিল যদিও এই পারস্পরিক নৈকট্য ছিল সাময়িক।
বস্তুতপক্ষে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রশ্নে রাশিয়া এবং ব্রিটেনের মধ্যে পুনরায় অবিশ্বাস দানা বাঁধে। ১৯৪২ সাল থেকেই স্তালিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য চাপ দিতে থাকে যাতে করে নাৎসী আক্রমণের চাপ কিছুটা হলেও রাশিয়ার উপর থেকে কমে। কিন্তু চার্চিল মনে করেছিলেন যে ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন কেউই সামরিকভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার জন্য প্রস্তুত নয় এবং তাছাড়া জার্মান আক্রমণের চাপে এমনিতেই রাশিয়ার সামরিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়বে, তাই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা অর্থহীন এবং ব্রিটেনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেবে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী মলোটভ প্রথমে ইংল্যান্ড এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং চার্চিল এবং রুজভেল্টকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলে ১৯৪২ সালের মধ্যেই জার্মানির পতন ঘটবে। মলোটভের এই প্রস্তাবে রুজভেল্ট রাজি হলেও চার্চিলের আপত্তির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে মতভেদ ছিল ঠান্ডা লড়াই এর পটভূমি।
 |
| মলোটভ (Vyacheslav Mikhaylovich Molotov) |
অতঃপর ১৯৪৩ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত তেহেরান সম্মেলনে চার্চিল, স্তালিন এবং রুজভেল্টের উপস্থিতিতে ঠিক হয় যে কালবিলম্ব না করে মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনেক পরে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই জুন (যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে মুক্তি দিবস বা ‘Deliverance Day’ নামে পরিচিত) বহু প্রত্যাশিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে ফ্রান্সের মাটিতে প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার মিত্রপক্ষীয় সেনা অবতরণ করে। এই রণাঙ্গন খোলার আগেই অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত রেড আর্মি নাৎসীদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। যাই হোক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে এই কালবিলম্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের প্রতি রাশিয়াকে ক্ষুব্ধ করেছিল। রাশিয়ার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরী করে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড রাশিয়ার সম্পদকে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল।
আকস্মিক নাৎসী আক্রমণের সামনে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে সামরিক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি লাভ করলেও বাস্তবে রাশিয়ার তাতে কোন লাভ হয়নি। ১৯৪১’র অক্টোবরে ঠিক হয়েছিল যে রাশিয়াকে প্রতি মাসে ৪০০ উড়োজাহাজ, ৫০০ ট্যাঙ্ক, অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, ইস্পাত, তামা, তেল প্রভৃতি দ্রব্য দিয়ে সাহায্য পাঠানো হবে। কিন্তু এই সব সাহায্য সরাসরি রাশিয়াতে প্রেরণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুত রাখা হয়েছিল এবং পাঠাতে অনেক দেরী করা হয়েছিল। এরপরেও ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত মস্কো সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল রাশিয়ার প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।
রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন অন্যদিকে হাল আবেগপ্রবণ হয়ে মন্তব্যও করেছিলেন যে এখন থেকে আর কূটনৈতিক জোট গঠন, প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপন অথবা শক্তিসাম্যের রাজনীতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু রুজভেল্ট এবং হালের এই প্রত্যশা পূরণ হয় নি কেন না ফলে ১৯৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় একক শক্তিতে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করে আত্ববিশ্বাসে বলীয়ান কমিউনিস্ট রাশিয়া, বিশেষত স্ট্যালিন পশ্চমী শক্তিবর্গের প্রতি আর আপোষের নীতি গ্রহণ করতে রাজি ছিল না।
হার্বাট ফিস ‘The Three who led’ প্রবন্ধে লিখছেন যে সামরিক সাফল্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালিনের মনোভাব ক্রমশ অনমনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩’র আগস্ট মাসে কুইবেক সম্মেলনের প্রাক্কালে মার্কিন যুদ্ধ বিভাগের একটি প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে জার্মানির পতনের পর যুদ্ধাবসানে রাশিয়া ইওরোপ মহাদেশের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হবে।
শীতল যুদ্ধের সারাংশ ছিল যুদ্ধকালীন তিনটি শীর্ষ সম্মেলনে – তেহেরান (নভেম্বর, ১৯৪৩), ইয়াল্টা (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫) এবং পোটসডম (জুলাই ১৯৪৫) নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সম্পর্কের অভিঘাতকে প্রকাশিত করে। একদিকে তেহেরান সম্মেলনের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য রোধ করার জন্য গ্রীস বন্ধান অঞ্চলে একটি পৃথক রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব দেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তিতে (তারা ভেবেছিল যে ইংলিশ চ্যানেলের দিক দিয়ে ব্যাপক অভিযান চালালে তাড়াতাড়ি জয় আসবে) তা খোলা সম্ভব হয় নি এবং এর ফলে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয়।